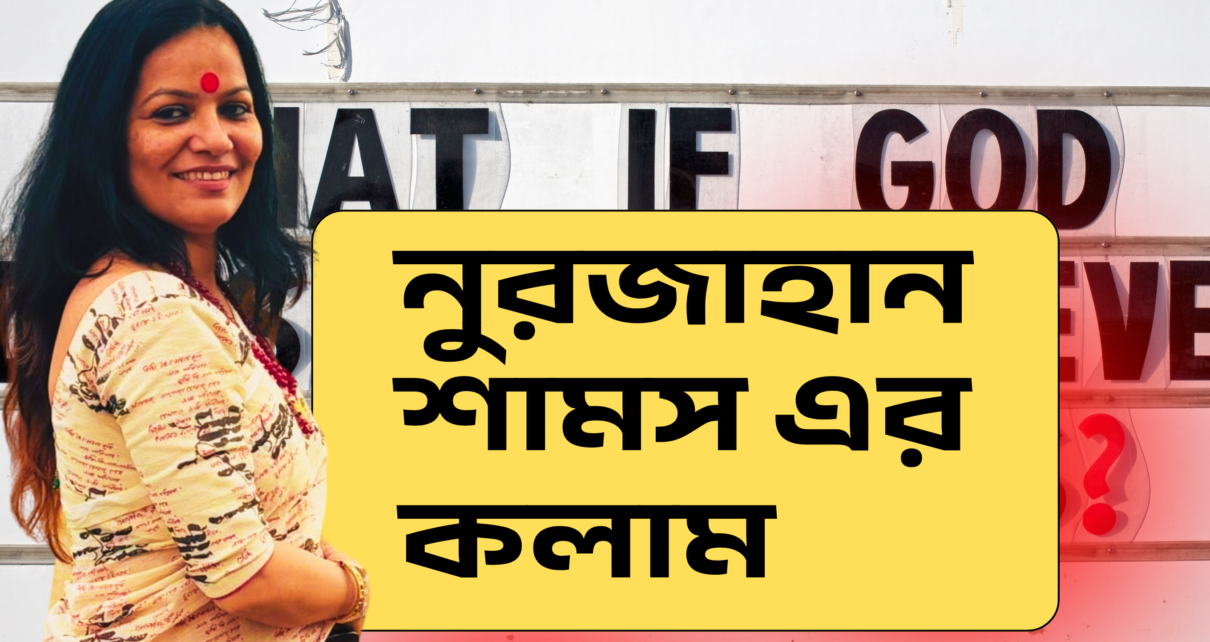নুরজাহান শামস, অস্ট্রেলিয়া | 15th May 2025
বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান ঘোষণা করেছিল স্বাধীনতার পর; “ধর্ম যার যার, বিশ্বাস যার যার” ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে জায়গা পেতে শুরু করেছিলো। তবে গত কয়েক দশকে ধর্মীয় মৌলবাদিতা অর্থাৎ ধর্মের বইবচনের অধিকার, ধর্মান্ধতা, সামিল সংগঠন, দৃষ্টিভঙ্গার একগুঁয়েমি এবং ধর্মকে রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের প্রবণতা বেড়ে গেছে। এই প্রবণতা শুধু ধর্মবিরোধীদেরই নয়, গোটা সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে; রিপোর্ট করায়, চিন্তা প্রকাশ করায়, নাস্তিক বা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তির জীবন—শান্তি ও নিরাপত্তায় গ্রাস করেছে মৌলবাদীদের আগ্রাসন।
নিচে আমরা বিশ্লেষণ করবো:
- ধর্মীয় মৌলবাদিতা কীভাবে গড়ে উঠেছে, কোথায় কোথায় তার ধরন দৃশ্যমান;
- নাস্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষদের উপর আক্রমণ, বাধা ও আইনি-সামাজিক প্রতিবন্ধকতা;
- রাষ্ট্র ও আইন কি ভূমিকা নিচ্ছে, বা নিচ্ছে না;
- এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের সম্ভাবনা ও করণীয়।
১. ধর্মীয় মৌলবাদিতার উত্থান: ইতিহাস ও বর্তমান
ইতিহাস ও সামাজিক ভিত্তি
- ঔপনিবেশিক কাল ও পরিচিতি: ব্রিটিশ ভারতের সময় ধর্মভিত্তিক পরিচয়ের শক্তি গড়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলিম ভাবাবেগ, সম্প্রদায় ভিত্তিক স্বনিয়ন্ত্রিততা, এবং ধর্মীয় অনুভব সমাজে শক্তিশালী ছিল। স্বাধীনতার পরও এসব অনুভূতি সম্পূর্ণ খর্ব হয়নি।
- রাজনীতি ও ধর্ম: স্বাধীনতার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতা ধর্মের অনুভূতিকে রোহানি ও সাংস্কৃতিক অনুমতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ধর্মীয় স্বরাষ্টার স্বীকারোক্তি পেতে রাজনৈতিক দলগুলো মৌলবাদী সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছে বা তাদের দিক থেকে সমর্থন পেতে পয়েরচেষ্টা করেছে।
- শিক্ষা, মিডিয়া ও সংস্কৃতি: কিছু ধর্মীয় স্কুল বা মাদরাসা, কিছু ধর্মীয় পরিচালিত মিডিয়া, প্রচারনায় ধর্মান্ধতা ও অপরাধমূলক বোঝা সৃষ্টি করেছে। বর্ণবৈষম্য, নারী ও মহিলা বিষয়ক অধিকার, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গা সবখানেই ধর্মের আড়ালে বৈষম্যের সুবিধা হয়েছে।
সাম্প্রতিক সময়ে দৃশ্যমান ধরণ
- ধর্মীয় মৌলবাদ যত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, তার ধরন বিভিন্ন: ধর্মান্ধ মিলিত সমাজসেবামূলক কাজ, ধর্মবিশ্বাসের নামে আইন ও নীতি প্রণয়ন, ধর্মনির্ধারিত সামাজিক আচরণবিধি জোরদার করা, ধর্মানুভূতির “অপমান” বা “অভিযোগ” বিষয়ক আইন ব্যবহার।
- ধর্মান্ধ/মৌলবাদী সংগঠনগুলো মোবাইল, ইন্টারনেট ব্যবহার করছে ধর্মান্ধ এবং নিষিদ্ধ সাহিত্য, ব্লগ, কথা বলার স্বাধীনতা দমন করতে। ব্লগার, লেখক, শিক্ষক, চিন্তাবিদ যারা ধর্মকে প্রশ্ন করেন, তারা বেছে বেছে টার্গেট হচ্ছেন। Dhaka Tribune+2DW News+2
২. নাস্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও মুক্তচিন্তার ব্যক্তিদের সমস্যা: ভয়, দমন, মৃত্যু
সামাজিক দমনে পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক
- পরিবারের মধ্যেই নাস্তিকতা ঘটনা জানলে শিশুশিক্ষায়, পারিবারিক বন্ধনে নানান রকম চাপ পড়ে। অনেকেই সামাজিকভাবে লজ্জিত হতে হয়, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়দের দ্বারা অপমানিত হতে হয়, সমাজে বিচ্ছিন্নতার ভয়ে নিজের মতামত গোপন রাখে।
- সামাজিক “নিয়ম” বা সাংস্কৃতিক প্রত্যাশা: ধর্মীয় পোশাক, ধর্মীয় আচরণ ও ধর্মীয় মিথস্ক্রিয়া কঠোরভাবে পালন করা হয়। ধর্মবহির্ভূত আচরণ বা ধর্মকে প্রশ্ন করা হলে গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্তির ভয় থাকে।
আইনি ও রাষ্ট্রীয় বাধা
- ধর্মীয় ভাবাবেগকে আঘাত করার আইন: বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ধারাগুলো যেমন “ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত” বা “অপমান” (Section 295A, Section 298) ইত্যাদি যা বিশেষ ধর্মের বিশ্বাস বা ধর্মানুভূতিকে আঘাত করা হয়েছে এমন বক্তব্য দণ্ডনীয় করে। Planner S M Saifur Rahman+2National Secular Society+2
- ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন (DSA), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন (ICT Act): এই আইনের মাধ্যমে অনলাইনে “ধর্মীয় ভাবাবেগ আঘাত করা” বিষয়ক অভিযোগে ব্লগার, নাস্তিক, মুক্তচিন্তার লেখকরা মামলা, গোপন হয়রানি, গ্রেফতার, হয়তো অভিযোগে ফাঁসানো হয়। fln.dk+3National Secular Society+3Planner S M Saifur Rahman+3
- সশস্ত্র হামলা, হত্যাকাণ্ড: ২০১২‑২০১৫ সালের মধ্যে ব্লগার, লেখক, প্রকাশক যারা ধর্মীয় মৌলবাদিতা বা ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন, তাদেরকে মারধর, হত্যার হুমকি এবং কিছু ক্ষেত্রে হত্যাই করা হয়েছে। উদাহরণ: Avijit Roy, Asif Mohiuddin, Ahmed Rajib Haider, Niladri Chattopadhyay‑সহ আরো অনেকে। Dhaka Tribune+2National Secular Society+2
- নিজের নিরাপত্তা, নির্বাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ: অনেক ব্লগার দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন; বা নিজের পরিচয় গোপন রেখে কাজ করছেন; অনেকেই আত্মনিয়ন্ত্রণ করেন, কঠিন বা বিতর্কিত বিষয় তারা এড়িয়ে যাচ্ছেন, নিজে‑নিজে সাইলেন্স বা সেন্সরশিপ করে নিচ্ছেন। Planner S M Saifur Rahman+1
রাষ্ট্রের ভূমিকা ও দ্বিমুখিতা
- সরকার অনেক সময় মৌলবাদীদের কাছ থেকে রাজনৈতিক ঝুঁকি এড়িয়ে ধর্মানুভূতির অভিযোগ উঠলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে অস্বীকৃতি জানায় বা মাঝেমধ্যে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করতে দেরি হয়। কখনো কখনো সরকার নিজেই ধর্মানুভূতিকে রাজনৈতিক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে।
- আইন প্রয়োগে দ্বিচারিতা: যদি ধর্মানুভূতির অভিযোগ উঠুক ক্ষমতাসীন ধর্মপন্থীদের বিরুদ্ধে, আইন হয়তো দীর্ঘমেয়াদী এবং কার্যকর হয় নাও; অন্যদিকে ধর্মনানুভূতির অভিযোগে সরকার তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নিতে পারে।
- সংবিধান ও আন্তর্জাতিক চুক্তি: সংবিধান বাংলাদেশে ধর্মের স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে; দেশের কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিতে সই করেছে যা চিন্তা, ধর্মবিশ্বাস, প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত করে। কিন্তু বাস্তবে এসব অধিকারের প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ। ibka.org+1
৩. ধর্মীয় মৌলবাদ ও নাস্তিক বিরোধিতার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব
স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা
ধর্মবিরোধী বা ধর্মের প্রশ্ন করা বিষয়গুলো শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গা বিকাশ পায় না; গবেষণার স্বাধীনতা কমে গেছে, কেউ ধর্মের নাজুক দিকগুলো বিশ্লেষণ করতে ভয় পায়। বিজ্ঞান, তত্ত্ব, ইতিহাস নিয়ে আলোচনা চরম সীমিত হয়।
গণমাধ্যম ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম
অনেক অনলাইন ব্লগ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুক্ত চিন্তার জন্য কিছু জায়গা সৃষ্টি হলেও ব্লগার, লেখক, ইউটিউব রচিত বিষয়বস্তুకి হামলা, হ্যাকিং, ডি-মনিটাইজেশন, ব্লকিং, ডিজিটাল আইনে অভিযুক্ত করা হয়। অনেকে বিদেশে গিয়ে কাজ করতে বাধ্য।
সংখ্যালঘু ধর্ম ও সম্প্রদায়
হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও আহমদিয়া সম্প্রদায়সহ ধর্ম সংখ্যালঘুদের প্রতি মৌলবাদীদের সহিংসতা বা হয়রানি বেড়েছে। মন্দির, গীর্জা, বৌদ্ধ বিহার হামলার ইতিহাস রয়েছে (যেমন রামু দাঙ্গা ২০১২ সালে) যেখানে ধর্মীয় অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। Wikipedia+1
লোকনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিশ্বাস
এসব ঘটনা আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশকে একটি এমন দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে যেখানে মুক্ত বিবেক, মতপ্রকাশ ও ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য ঝুঁকি রয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী আবেদনকারী যারা ধর্মের কারণে বিপদে রয়েছেন, তাদের বিষয়ে বিদেশি সরকারের নীতি নজর দিচ্ছে। GOV.UK+1
৪. রাষ্ট্রীয় ও আইনগত পর্যালোচনা: কি হচ্ছে, কি হওয়া উচিত
বর্তমান আইন ও মনোভাব
- আইন: দণ্ডবিধা (sections যেমন 295A, 298) আছে, ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন ও ICT আইন আছে, যা কখনো কখনো ধর্মনানুভূতির অভিযোগ তুলে বিষয়গুলো অনলাইন রাজ্যে নিয়ন্ত্রণে রাখে। Planner S M Saifur Rahman+2GOV.UK+2
- সংশোধন বা মনোভাবের পরিবর্তন: কিছু আইন সংশোধনের দাবি উঠেছে, মানবাধিকার সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংগঠন বলছে DSA, ICT আইন ইত্যাদি আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে মিলছে না। সরকারের কিছু উচ্চ পর্যায়ের বক্তৃতায় বলেছেন মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রয়োজন; কখনো কখনো মৌলবাদী হামলার নিন্দা করে; আবার কখনো ধর্মনানুভূতির “অভিযোগ” কে সামনে এনে মুক্তমতকে সীমিত করার কথা বলা হয়। National Secular Society
- নিরাপত্তা ও অভিযোজন: নিরাপত্তা বাহিনী, বিচার ব্যবস্থা ও সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা মাঝে মাঝে মৌলবাদী হামলার তদন্ত শুরু করে, কিছু অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনানুগ মামলা হয়; কিন্তু বিচার ও অপরাধীর দণ্ড অনেক সময় অনিশ্চিত, বিচার বিচারব্যবস্থা দেরিতে কাজ করে বা সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহে সমস্যা থাকে।
কি হওয়া উচিত
নিচে কিছু সুস্পষ্ট ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা উদ্যোগ দেওয়া হলো:
- আইনগত সংস্কার
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন ও দণ্ডবিধার ধর্মনানুভূতির আইনগুলো সংশোধন করে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হোক — কি “ধর্মনানুভূতির আঘাত”, কি “অপমান” — যেন অস্পষ্টতা ও গুপ্ত অপব্যবহার বন্ধ হয়।
- বিবেক, মতপ্রকাশ ও ধর্ম/অধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতা সংবিধানে ও আইনগতভাবে আরও শক্তভাবে রক্ষা করা হোক।
- বিচারব্যবস্থা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা
- ধর্মনানুভূতির অভিযোগে মামলা হলে দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক। হামলা ও হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে দায়ীদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা হোক।
- ব্লগার, প্রার্থক ধারার মতপ্রয়াত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা, নিরাপদ আশ্রয় বা নির্বাসন সুযোগ দেওয়া হোক।
- সামাজিক সচেতনতা ও শিক্ষা
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মনিরপেক্ষতার গুরুত্ব শেখানো হোক, মুক্তচিন্তা ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়া হোক।
- মিডিয়া ও সাহিত্য/সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব বিভিন্ন মতের সম্মান ও Pluralism প্রচার করা হোক।
- সামাজিক সংলাপ এবং বাস্তুতন্ত্র তৈরি
- ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সংলাপ বাড়াতে হবে — পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং মানুষের মৌলিক অধিকারকে সম্মান করার ভিত্তিতে।
- স্থানীয় সামাজিক নেতাদের ভূমিকা রাখা উচিত যারা ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে কথা বলবেন, সহনশীল সংস্কৃতি গড়ে তুলবেন।
- আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও মানবাধিকার সংস্থা
- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও বন্ধু দেশগুলোর চাপ দেওয়া উচিত বাংলাদেশের সরকারের প্রতি যেন তারা মৌলিক মানবাধিকার প্রয়োগে অগ্রগতি দেখান।
- শরণার্থী আইন, ভিসা ও অভিবাসন নীতি এই বিষয়ে সংবেদনশীল হবে যেন যারা ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মবিরোধের কারণে বিপদে রয়েছেন তারা নিরাপদ আশ্রয় পেতে পারেন।
৫. সিদ্ধান্ত: এক মুক্ত ও সহনশীল বাংলাদেশ গঠনের আহ্বান
বাংলাদেশ একটি বহু ধর্মের, বহু সংস্কৃতির দেশ। এখানে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, আহমদিয়া, এবং ধর্মনিরপেক্ষ ও নাস্তিক মানুষ পাশাপাশি বাস করে — কিন্তু ধর্মান্ধতার উত্থান যদি অব্যাহত থাকে, মুক্তচিত্ত ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা পুরোদমে বিপন্ন হবে। একটি সমাজ যেখানে মানুষ ধর্মনির্ধারিত নিয়মে বাধ্য হয়, যেখানে প্রশ্ন করা যায় না, যেখানে নাস্তিক হওয়া, ধর্ম পরিবর্তন বা ধর্মকে প্রশ্ন করা কঠিন হবে, সেখানে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠতে পারে না।
আমাদের উচিত হবে ভয়কে জয় করা, দ্বিমতকে সম্মান করা, পার্থক্যকে প্রশংসা করা। ধর্মই মহান যখন সেটি মানবতার জন্য কাজ করে; কিন্তু যখন ধর্ম অন্যের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাকে দমন করে, তখন সেই ধর্মের প্রয়োগ মূল্যায়নযোগ্য হওয়া উচিত।
শব্দসংখ্যায় ২০০০ ছাপিয়ে যেতে পারিনি হয়তো, তবে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হলো। আশা করি, এই ব্লগ পাঠকের মনে চিন্তার উত্তাপ এবং পরিবর্তনের প্রতি আহ্বান জাগাবে।